সঞ্জয় হাজরা
আদত নাম জৈসলমের, বাঙালি ডাকে জয়সলমির নামে। জোধপুর থেকে ভোরেই বেরিয়ে পড়লাম জয়সলমিরের উদ্দেশে। আজ পাড়ি দিতে হবে ২৮০ কিলোমিটার। তবে রাজস্থানের পথঘাট অত্যন্ত সুন্দর। সড়কযাত্রায় ধকল কার্যত নেই।
১৭১ কিলোমিটার পথ যাওয়ার পর এল পোখরান – ভারতের পরমাণু পরীক্ষণের জন্য সুপরিচিত। থর মরুভূমির বুক চিরে চলেছি। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। পথের মাঝে দেখা মিলল ময়ূর। আর মরুভূমির জাহাজ উট তো আছেই। এ ছাড়াও চিঙ্কারা হরিণ-সহ নানাবিধ মরু-জীবেরও সাক্ষাৎ মিলছে।

এক সুহানা সফরের অনন্য অভিজ্ঞতা ঝুলিতে ভরে পৌঁছে গেলাম জয়সলমির।পথের পাশেই পড়ল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংগ্রহশালা। এখানে রাখা আছে ভারত-পাক যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা সামগ্রী-সহ পাক সেনাবাহিনীর ফেলে যাওয়া নানা যান।
এর পর সোজা চলে গেলাম ‘গদিসর লেক’ দেখতে। এই কৃত্রিম জলাশয়টি ১১৫৬ সালে তৈরি করেন জয়সলমিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রাওয়াল জয়সল। তখন এর নাম ছিল জয়সলসর লেক। প্রায় দু’শো বছর পরে এই লেকটি নতুন করে সংস্কার করেন গদসি সিং। তার পর থেকে এর পরিচিতি হয় ‘গদিসর লেক’ নামে। সুন্দর কারুকার্যমণ্ডিত তোরণ দিয়ে প্রবেশ ‘গদিসর লেক’-এ। লেকের উত্তর ও পুবে ঘাটের সারি, লেকের মাঝে রয়েছে ছত্তিশ, চারপাশে নানা মন্দির ও অন্য অনেক স্থাপত্য। জয়সলমিরে প্রথম দর্শনেই আপনি মুগ্ধ হবেন।

জয়সলমিরে আমাদের ঠেক ছিল যথারীতি রাজস্থান পর্যটনের হোটেল, হোটেল মূমল। মধ্যাহ্নভোজন সেরে আমরা সোজা চলে এলাম জয়সলমির ফোর্ট তথা সোনার কেল্লায়। মধ্যযুগের ঐতিহাসিক এই দুর্গটিকে ইউনেস্কো তালিকাভুক্ত করেছে একটি বিশ্ব ঐতিহ্য রূপে। এই দুর্গ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ‘লিভিং ফোর্ট’। অর্থাৎ বিশ্বে হাতে গোনা যে ক’টি প্রাচীন দুর্গে আজও বসতি রয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম সোনার কেল্লা।
সোনার কেল্লা দেখার আগে একবার কেল্লার ইতিহাসে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। এই কেল্লা গড়েই মরুভূমির বুকে নগরের পত্তন করেন রাওয়াল জয়সল ১১৫৬ সালে। সাধু এউসুলের নির্দেশমতো রাওয়াল জয়সল লোধুর্বা থেকে রাজ্যপাট তুলে আনেন জয়সলমিরে। সোনালি বালিয়াড়িতে তৈরি হয় ভাটি রাজপুতদের রাজধানী।
১২৯৩ সালে সুলতান আলাউদ্দীন খিলজির হাতে সোনার কেল্লার পতন ঘটলেও ৯ বছরের মাথায় তা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন ভাটি রাজপুতরা। পরে মুঘল সম্রাট হুমায়ূন এক অভিযানের মাধ্যমে এই দুর্গকে দীর্ঘকাল মুঘল শাসনের অধীনস্থ করে রেখেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে তৎকালীন রাজপুত বংশধর মহারাওয়াল মুলরাজ এক চুক্তির মাধ্যমে ইংরেজদের কাছ থেকে দুর্গ পুনরায় ফিরে পেয়েছিলেন। তবে সেই রাজত্ব যে আগের মতো সার্বভৌম ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

ত্রিকূট পাহাড়ের বুকে হলুদ বেলেপাথরে নির্মিত এই ঐতিহাসিক দুর্গ। দুর্গটি অন্তত ২০ তলা উচ্চতাবিশিষ্ট। কোথাও কোথাও উচ্চতা তার চেয়েও বেশি। দুর্গের দৈর্ঘ্য ১,৫০০ ফুট এবং প্রস্থ ৭৫০ ফুট। এর প্রতিটি দেয়ালে রয়েছে তিন স্তর বিশিষ্ট মজবুত গাঁথুনি। ভেতরে প্রবেশের জন্য রয়েছে চারটি সুবৃহৎ দরজা। অক্ষয় পোল দিয়ে প্রবেশ। তার পর একে একে সুরজ পোল, গণেশ পোল, হাওয়া পোল পেরিয়ে দশেরা চক। এখানকার দশেরা গগৌঁর বিখ্যাত। সমগ্র দুর্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দাঁড়িয়ে আছে ৯৯টি সুদৃশ্য গম্বুজ।
হলুদ বেলেপাথরের উপর আকর্ষণীয় মধুরাঙা কারুকার্য। যে কারণে সূর্যালোকে এই দুর্গটি সোনা রঙ ধরে। তাই এই দুর্গ ‘সোনার কেল্লা’, ‘স্বর্ণের দুর্গ’, ‘স্বর্ণের শহর’ ইত্যাদি নামে খ্যাতি পেয়েছে। তবে বরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের অনন্য সৃষ্টি ‘সোনার কেল্লা’ সিনেমার পরে জয়সলমির দুর্গের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে যায়। গাইডের সঙ্গে দুর্গ ঘুরে দেখলে তারও প্রমাণ মেলে। গাইডই বলেন, ‘এটা মুকুলের বাড়ি’, ‘এটা রতনের বাড়ি’ ইত্যাদি। মুকুলকে মনে পড়ছে তো? ‘সোনার কেল্লা’র চরিত্র। আর রতন হল মুকুলের পূর্বজন্মের বন্ধু।

জয়সলমির দুর্গ এক ভিন্ন চরিত্রের অধিকারী। সে কখনও একাকী নির্জনে রাত কাটায় না। সারা বিশ্বের যে গুটিকয়েক বিশ্ব ঐতিহ্যে এখনও মানুষ বসবাস করে, তার মধ্যে জয়সলমির দুর্গ অন্যতম। ভাটি রাজপুতদের বংশধররাই পরম্পরায় সেখানে বসবাস করছে। এর জন্য তাদের কোনো অর্থ কিংবা ভাড়া প্রদান করতে হয় না। বর্তমানে সেখানে দুই থেকে তিন হাজার মানুষ বসবাস করছে। ২০১৩ সালে ইউনেস্কো একে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত করলেও তাদের বসবাস অব্যাহত আছে। এখনও সোনার কেল্লার অভ্যন্তরে ১২ শতকের অনেক প্রথা ও সংস্কৃতি চালু আছে।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, তৎকালীন সময়ে দুর্গটিতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করত। রাজার উপদেষ্টারা ও রাজ্যের শিক্ষকগণ দুর্গে বসবাস করার সুযোগ পেতেন। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এই নিয়ম পুরোপুরি বলবৎ ছিল। এখন তাঁদের উত্তরাধিকাররাই সেখানে বসবাস করছেন। ইতিমধ্যেই এই দুর্গ ৯টি শতাব্দী অতিক্রম করেছে। এখানে কাটিয়ে গিয়েছে ২৩টি প্রজন্ম। আপাতত এখানে এখন যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা সকলে এখানেই জন্মেছেন, বড়ো হয়েছেন এবং এখানেই কাজ করছেন। অনেকে বাণিজ্যিক কারণে নিজেদের বাসস্থানের একাংশকে দোকান, ক্যাফে ও আবাসিক হোটেলে পরিণত করেছেন।
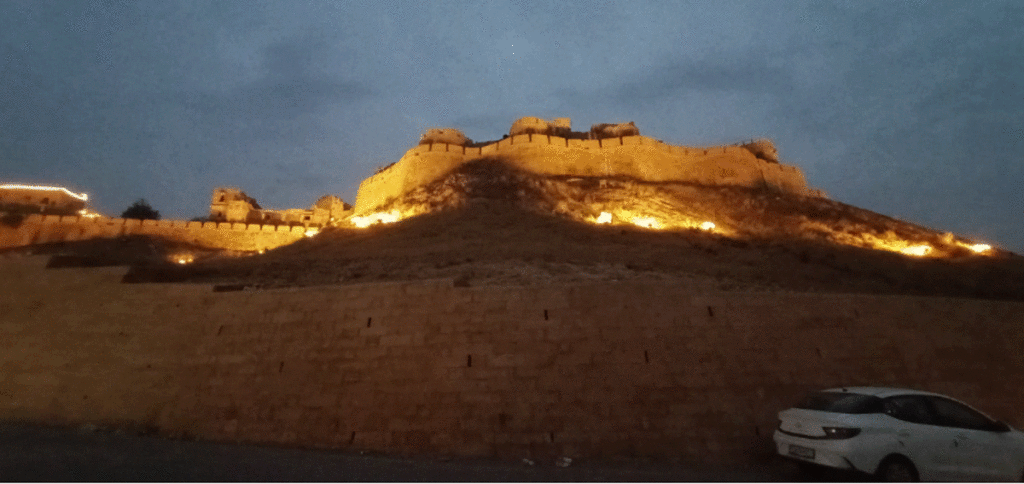
সম্পূর্ণ ভাবে দুর্গটি ঘুরে দেখতে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। ভালো করে বুঝে দেখার জন্যে গাইড থাকাটা আবশ্যিক। দুর্গের উপর থেকে নীচের জয়সলমির শহরটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে জনআধিক্য কী ভাবে বেড়েছে। তবে আজ আর নয়। কারণ এ বার সফরের ক্লান্তি শরীরকে ধীরে ধীরে গ্রাস করছে। তাই আজকের মতো বিশ্রাম।
পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে ফের জয়সলমিরের পথে বেরিয়ে পড়লাম। একে একে দেখে নিলাম ‘পাটওয়ন কি হাভেলি’, ‘নাথমলজি কি হাভেলি’, ‘সলিম সিং কি হাভেলি’ এবং ‘মহারাজা প্যালেস’ দেখতে। প্রতিটি হাভেলিতেই রয়েছে খুব সুন্দর জাফরির কাজ। আপনাকে আকর্ষণ করবেই। হাভেলি-মালিকদের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের সম্ভার সুরক্ষিত করে রাখা আছে। এ ছাড়া পুরো প্যালেস জুড়ে রয়েছে অপূর্ব সুন্দর রংবেরঙের কাচের কাজ। এত সব জমকালো আর সুন্দর শিল্পকর্ম দেখে আপনি মুগ্ধ হবেনই।

এর পরে দুপুরের খাওয়া সেরে বেরিয়ে পড়লাম স্যাম মরুভূমির পথে। আমাদের প্রথম গন্তব্য ছিল পরিত্যক্ত গ্রাম কুলধারা। শুধু সাহিত্যের পাতায় নয়, বাস্তবেও ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে বহু ‘ক্ষুধিত পাষাণ’। সে রকমই একটি কুলধারা। সোনার কেল্লার শহর থেকে ১৮ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে এই স্থান অতীতে ছিল বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কোনো এক রহস্যজনক কারণে রাতারাতি তা পরিত্যক্ত হয়ে যায়। সারি সারি ঘর-রাস্তা-মন্দির নিয়ে একা একা পড়ে আছে অতীতের এই জনপদ। শুধু সেখানে থাকার কেউ নেই।
থর মরুভূমির কোলে এই গ্রামের পত্তন হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। জোধপুরের পালিওয়াল সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণরা এখানে বসত গড়েছিলেন। তাঁরা কৃষি ও ব্যবসা, দু’টি কাজেই দক্ষ ছিলেন। পালি থেকে এসেছিলেন বলে তাঁদের পালিওয়াল ব্রাহ্মণ বলা হত। ১৮৯৯ সালে রচিত বই ‘তারিখ-ই-জয়সলমের’-এ উল্লেখ আছে কুলধারার। সেখানে বলা হয়েছে, কড়হান নামে এক পালিওয়াল ব্রাহ্মণ এখানে প্রথম বসত তৈরি করেন। গ্রামের ধ্বংসস্তূপে পাওয়া গিয়েছে তিনটি সমাধিক্ষেত্র। পাশাপাশি, ৬০০-র বেশি বাড়ির ভগ্নাবশেষ সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কুলধারা-সহ স্থানীয় ৮৩টি গ্রামে জনবসতি গড়ে উঠেছিল। জনশ্রুতি, ১৮২৫ সালে রাখিপূর্ণিমার রাতে জনশূন্য হয়ে পড়ে সেগুলো। রাতারাতি কর্পূরের মতো মিলিয়ে যান প্রায় ১৫০০ গ্রামবাসী। তবে বাকি গ্রামগুলোর নাম চাপা পড়ে গিয়ে মূলস্রোতে রয়ে গিয়েছে শুধু ‘কুলধারা’ নামটিই।
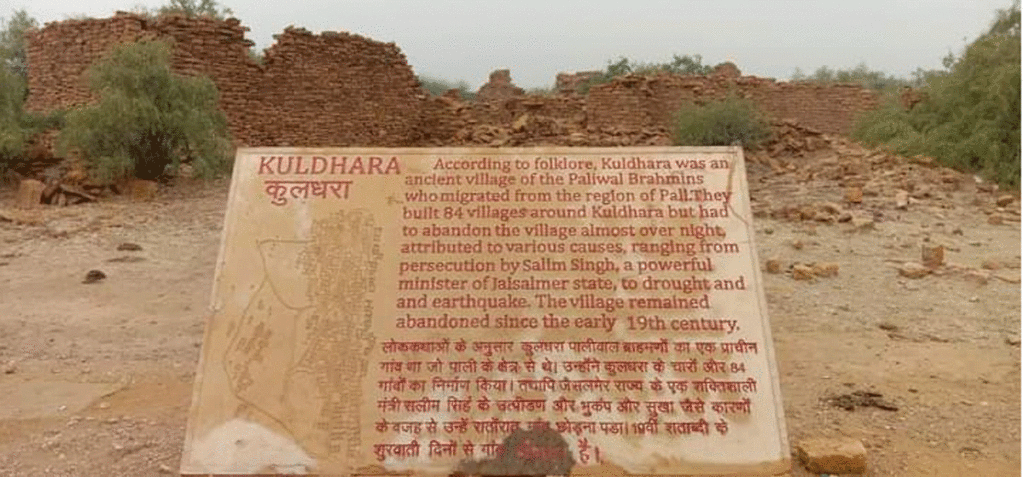
কেন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে কুলধারা? নেপথ্যে আছে বহু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তি। সে রকমই এক কাহিনি বলে, স্থানীয় সামন্ত শাসক সলিম সিং নাকি গ্রামের এক মেয়ের প্রেমে পড়েছিলেন। তিনি সৈন্য পাঠিয়ে হরণ করতে চেয়েছিলেন ওই কন্যাকে। কিন্তু গ্রামবাসীরা এক রাত সময় চেয়ে নেন। বলেন, পরের দিন এলে তাঁদের হাতে মেয়েকে তুলে দেওয়া হবে। গ্রামবাসীদের ফন্দি বুঝতে পারেননি সামন্ত। তিনি অপেক্ষা করতে রাজি হয়ে যান। সেই সুযোগে এক রাতের মধ্যে পালিয়ে যান গ্রামবাসীরা। পরের দিন সকালে খুঁজে পাওয়া যায়নি তাঁদের একজনকেও। সামন্তের কুনজর থেকে রক্ষা পান গ্রামের মেয়ে।
কিন্তু গ্রামবাসীরা কি ফিরে যান আবার জোধপুরের পালিতে? নাকি নতুন বসতি গড়েন অন্য কোথাও? ইতিহাস সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব। কার্যত কর্পূরের মতো উবে যান তাঁরা। প্রায় সাড়ে পাঁচশো বছর ধরে তিলে তিলে গড়ে ওঠা কুলধারা ভৌতিক গ্রামে পরিণত হয়।
দিল্লির প্যারানর্মাল সোসাইটির দাবি, রাতভর এখানে অলৌলিক ঘটনা ঘটে চলে। আচমকাই নাকি কমে যায় তাপমাত্রা। রাতের অন্ধকার চিরে শোনা যায় আর্ত চিৎকার। বিশ্বাসীদের ধারণা, কুলধারার অতীত-বাসিন্দাদের আত্মা এখনও এই গ্রামের মায়া কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এ তো গেল জনশ্রুতি।

ঐতিহাসিক তথ্য কী বলছে? অনেক গবেষকের ধারণা, যুদ্ধের প্রয়োজনে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল গ্রামবাসীদের। তবে ঐতিহাসিক ও গবেষকদের বড়ো অংশের বিশ্বাস, খরার কারণেই জনহীন হয়ে পড়ে কুলধারা ও তার সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম। কুলধারার জলের উৎস ছিল ক্ষীণ কাঁকনি নদী আর গ্রামের কুয়ো। কিন্তু ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ শুকিয়ে আসতে থাকে গ্রামের কুয়োগুলি। ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে জল ছিল শুধু গ্রামের ধাপ-কুয়ো এবং আর দু’টি কুয়োতে। জলাভাবে কমে যায় কৃষিফলন। কিন্তু জয়সলমিরের রাজপুত শাসকদের জারি করা রাজস্বের হার কমেনি এক বিন্দুও। তা মেটাতে নাভিশ্বাস উঠে যায় গ্রামবাসীদের। ধীরে ধীরেই হোক, বা রাতারাতি, জনশূন্য হয়ে পড়ে কুলধারা গ্রাম। আর কেউ কোনো দিন ফিরে আসেননি এই গ্রামে। এখন আসেন পর্যটকরা। ইদানীং রাজস্থান পর্যটনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট স্পট কুলধারা। সোনার কেল্লার পাশাপাশি পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিচ্ছে ‘ভৌতিক’ কুলধারাও।
কুলধারা থেকে চলে এলাম খাবা দুর্গে। কথায় আছে না, ইতিহাস কথা বলে। তবে সে কথা শুনতে গেলে কান পাততে হয় তার সাক্ষী হিসাবে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা ইট-কাঠ-পাথরের গায়ে। কখনও তার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে থাকে অভিশপ্ত ও অত্যাচারের জীবনকাহিনি আবার কখনও বা সেখানে থাকে বীরগাথা কিংবা খ্যাতি আর ঐশ্বর্য্যের জৌলুস।
কুলধারা থেকে মাত্র ২১ কিলোমিটার দূরে খাবা হল এ রকমই এক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা জনমানুষহীন প্রাচীন দুর্গ এবং দুর্গ সংলগ্ন ভগ্ন গ্রাম। ১৩ শতকে প্রতিষ্ঠিত এই মরু-জনপদটি ছিল এক সময়ে এই অঞ্চলের সব চেয়ে বর্ধিষ্ণু জনপদ। কারণ সেই সময়ে ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য সিন্ধু অঞ্চলে যাতায়াতের যে পথ ছিল, সেই পথের উপরেই অবস্থিত ছিল এই জনপদ। আর এর বিস্তৃতি ছিল কুলধারা গ্রাম পর্যন্ত। থর মরুভূমির ওপরে অবস্থিত এখানকার দুর্গ থেকে চার পাশের গ্রামগুলির উপর নজরদারি করা হত।

৫০০ বছর ধরে প্রায় ১৮০০ পালিওয়াল ব্রাহ্মণ গ্রামবাসীর প্রতিষ্ঠিত এই গ্রামটি ছিল তৎকালীন সময়ে ধনঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু নিয়তির করুণ লিখনে মাত্র এক রাত্রিতে গ্রাম-সহ এই দুর্গটি শ্মশানপুরীতে পরিণত হয়। পরিত্যক্ত এই গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং ভগ্নপ্রায় দুর্গ ছাড়া আজ আর কিছু নেই। এখানকার কাহিনিতেও জড়িয়ে রয়েছে অত্যাচারী লোলুপ সামন্ত সলিম সিংয়ের নাম। তার কুনজর থেকে গ্রামের নারীদের আব্রু বাঁচাতে গ্রামপ্রধান ১৮২৫ সালের এক রাতে একটি জরুরি সভা ডেকে আশপাশের পরিবারগুলিকে নিঃশব্দে গ্রাম ত্যাগ করার পরামর্শ দেন। তাঁর সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সে দিন গ্রামবাসীরা গ্রাম ত্যাগ করে কোথায় গেলেন, কেনই বা পরে ফিরে এলেন না, সে বিষয়ে কোনো সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে সে যা-ই হোক না কেন, এই ঘটনা তৎকালীন সময়ে সামাজিক ঐক্যের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে।
বর্তমানে রাজস্থানের যে কয়েকটি ভৌতিক স্থান রয়েছে তার মধ্যে ভানগড় দুর্গ, কুলধারা গ্রাম অন্যতম। এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে খাবা দুর্গও।
খাবা ঘুরে চলে গেলাম ১৮ কিলোমিটার দূরের স্যাম বালিয়াড়িতে। জিপে চড়ে পৌঁছে গেলাম মরুভূমির অভ্যন্তরে। যেখানে প্রকৃতির সৃষ্টি ‘স্যান্ড ডিউনস’ বা বালিয়াড়ির মধ্যে দিয়ে সফরের অভিজ্ঞতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ওখানে গিয়ে উটের পিঠে চড়ে কিছুটা ভ্রমণ করতে ভুলবেন না। কারণ ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ুর সেই স্মৃতির সাক্ষী এখন আপনিও। মরুসফর হল, উটে চড়া হল। এ বার চলে এলাম আমাদের জন্য নির্ধারিত মরু-তাঁবুতে। এখানকার সন্ধেটা কেটে গেল রাজস্থানি লোকসংগীত আর লোকনৃত্যের জমজমাট আসরে। মরুভূমির তাঁবুতে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতাও অনন্য।

দু’ দিনের জয়সলমির সফর আমরা শেষ করেছিলাম এ ভাবেই। তবে আপনাদের হাতে সময় থাকলে ঘুরে আসতে পারেন ১৯৭১-এ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধখ্যাত লোঙ্গেওয়াল গ্রাম বা ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত। আজকের মতো বিদায় নিই। তৃতীয় পর্বে ফিরে আসব রাজস্থানের শৈলশহর মাউন্ট আবুর গল্প নিয়ে। (চলবে)
ছবি: লেখক
আরও পড়তে পারেন





